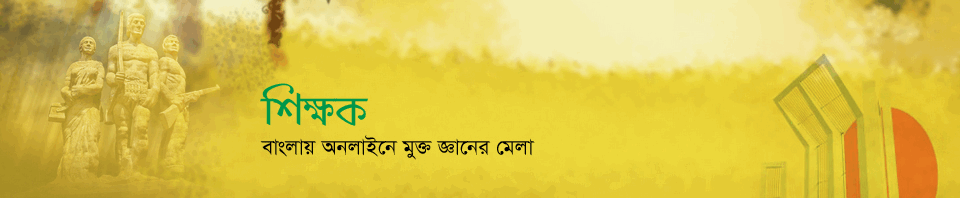লেকচার ভিডিওঃ
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি
পদার্থবিজ্ঞান একটা পরীক্ষণ নির্ভর বিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো দেখেন,পর্যবেক্ষণ করেন এবং এবং এদের মূলসুত্র ও সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করেন। আর প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর এই মুলসুত্র/প্যাটার্নই হল তত্ত্ব,নীতি,সূত্র। পদার্থবিজ্ঞানের যেকোনো তত্ত্ব নিছক কোনো কল্পনা বা অনুমান নির্ভর কোনো বিষয় নয়। প্রতিটি তত্ত্ব দীর্ঘদিনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা,প্রাকৃতিক ঘটনার পর্যবেক্ষণ,পদার্থবিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষিত সুত্র-নীতিসমুহের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তত্ত্ব, নীতি, পরীক্ষণ নিয়ে আমরা পরের লেকচারে আরেকটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এই লেকচারে আমরা আলোচনা করব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়ে।
পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশুনা শুরু করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কিভাবে কাজ করেন সেই সম্পর্কে একটা ধারনা রাখতে হবে। পদার্থবিদ্যা বা বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যই হলো আমাদের চারপাশের জগত সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। অনেকেই মনে করে থাকে আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাগুলো নিয়ে তত্ত্ব প্রদানের ব্যাপারটাই হল হলো বিজ্ঞান। ব্যাপারটা ঠিক তা না, যেমনটা মনে হয়। আমি অনেক ভেবেচিন্তে হোক আর এমনি এমনি হোক কিছু একটা বলে দিলাম, কাকতালীয়ভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা মিলেও গেল আর বাকীরা সবাই আর কোনো কথা না বলে তা মেনে নিল ব্যাপারটা এমনটা না। অনেক আগে এমন হত যে সমাজের জ্ঞানী-গুণী-গুরুত্বপূর্ণ মানুষরা কিছু একটা বলতেন আর বাকীরা সেটা বিনা বাক্যে মেনে নিত। এরিস্টটলের আমল থেকে হাজার বছর তাই হয়ে এসেছে। কিন্তু পরবর্তীতে পদার্থবিজ্ঞান হয়ে উঠে একটা পরীক্ষণ নির্ভর বিজ্ঞান। সভ্যতার শুরুর দিকের বিজ্ঞানী-দার্শনিকেরা যেভাবে কাজ করতেন তার পরবর্তী সময়ের বিজ্ঞানীরা অনেকটাই পরিবর্তিত ও কার্যকর পদ্ধতিতে কাজ করেছেন। গ্যালিলিও ছিলেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি কিনা প্রথম প্রকাশ্যে বলেছিলেন বিজ্ঞানের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, নিছক অনুমান কিংবা প্রাচীন বই, বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে নয়। পরবর্তী সময়ে নিউটন পাকিপাকিভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত করেন। কোনো নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে কিছু নেই। তারপরো সব বিজ্ঞানীরাই মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে কাজ করে থাকেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, সুনির্দিষ্ট পরিমাপ, পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষন; মোটামুটি এই কাজগুলোই তারা একটা সমন্বয়ের মাধ্যমে করে থাকেন। আর তারপর এই বিশ্লেষন থেকে তারা কিছু সিদ্ধান্তে আসেন। তারপর এই সিদ্ধান্তগুলো আরো পরীক্ষানীরিক্ষা, বিশ্লেষনের ধাপ পেরোয় তাদের গ্রহনযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। মোটামুটি এটাই হল বিজ্ঞানীদের কাজের প্যাটার্ন। গ্যালিলিওর পরবর্তী সময় থেকে বিজ্ঞানীরা কমবেশী এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই অনুসরণ করে এসেছেন। পদার্থবিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণার প্রতিটি ধাপেই রয়েছে সৃজনশীলতা। একজন পদার্থবিজ্ঞানীকে জানতে হয় কিভাবে কোন প্রশ্নটিকে সামনে রেখে এগুতে হবে, কিভাবে তার পরীক্ষাটি সাজাতে হবে, কিভাবে পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে বিশ্লেষনের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা করতে জ্ঞান, দক্ষতা, ভাগ্য, কল্পনাশক্তি, অনুমানশক্তি, বার বার পরীক্ষা, পরীক্ষার ভুল সংশোধন, ধৈর্য্য-এই সব কিছুই লাগে। অনেক সময় প্রচলিত ধারার বাইরে এসেও চিন্তা করতে হয়। এমনও হয় দীর্ঘ দিন, বছরের পর বছর গবেষণায় কোনো সাফল্য আসে না। আবার কোনো এক সময় হঠাৎ করে ঢেউয়ের মত একটার পর একটা আসতে থাকে সাফল্য।
এই আধুনিক সময়ের বিজ্ঞানীরা আগের তুলনায় অনেক কার্যকর পদ্ধতিতে গবেষণা করে থাকেন। এখনকার পরিক্ষণ ও গবেষণা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপুর্ণ দিক হল গবেষণা বা পরিক্ষণ শুরু করার আগে বিজ্ঞানীরা পরিবেশের উপর এর প্রভাব ও ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে আগেই অনেকদুর ভেবে রাখেন এবং সম্ভাব্য ঝঁকিগুলো এড়িয়ে চলেন। সবমিলিয়েই বিজ্ঞানীদের কাজ করার প্রক্রিয়াটাকে একটা কাঠামোয় আনা যায় যেটাকে আমরা বলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সেটার ধাপগুলোকে নিচের মত করে সাজানো যায়।

১.সমস্যাঃ এই ধাপে যে সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়।
২.তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণঃ এই ধাপে সমস্যাটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করা হয়।
৩.আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহনঃ তথ্য বিশ্লেষণ করে এই ধাপে সমস্যার সমাধান বা গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে একটা অনুমিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
৪.পরীক্ষার পরিকল্পনাঃ অনুমিত সিদ্ধান্ত কিভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হবে সে বিষয়ে এই ধাপে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এই ধাপে ডিজাইন/সেট করা হয়।
৫.পরীক্ষণঃ এই ধাপে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাটি করা হয়।
৬.ফলাফল বিশ্লেষণঃ পরীক্ষার ফলাফলগুলো এই ধাপে বিশ্লেষণ করা হয়। যদি ফলাফলের সাথে অনুমিত সিদ্ধান্ত মিলে যায় তাহলে ৯ নাম্বার ধাপে যেতে হয়। নতুবা ধাপ ৭ এ যেতে হয়।
৭.আনুমানিক সিদ্ধান্ত বর্জন/সংশোধনঃ পরীক্ষার ফলাফল থেকে যদি দেখা যায় যে ৩য় ধাপের অনুমিত সিদ্ধান্ত ভুল ছিল, তাহলে সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করা হয়।
৮.নতুন আনুমানিক সিদ্ধান্তঃ এই ধাপে নতুন অনুমিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরপর ধাপ ৪ এ ফিরে যেতে হয়।
৯.সিদ্ধান্ত গ্রহনঃ এই ধাপে গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
১০.ফলাফল প্রকাশঃ গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
উপরের ধাপগুলো থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটা প্যাটার্ন আমরা পাই।
১।সমস্যা নির্দিষ্টকরণ
২।সমস্যাটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
৩।অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহন
৪।পরীক্ষার পরিকল্পনা, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই।
৫।ফল প্রকাশ।
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতিটি ধাপেই গবেষক বা গবেষণা সংস্থার দক্ষতা, সৃজনশীলতা, অভিজ্ঞতার প্রকাশ পায়। এভাবে কাজ করতে করতেই একজন নবীণ গবেষকও ধীরে ধীরে গবেষণায় অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। সাধারণত দুই ধরনের বিজ্ঞানী দেখা যায়। এক হলেন যারা পরীক্ষার ফলাফল ও তথ্য বিশ্লেষণ করে মূলনীতি/তত্ত্ব প্রদান করেন। আরেকদল হলেন যারা কোনো তত্ত্ব সিদ্ধান্তকে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করেন, এর সীমাবদ্ধতা ও গ্রহনযোগ্যতা পরীক্ষার মাধ্যমে বের করেন।