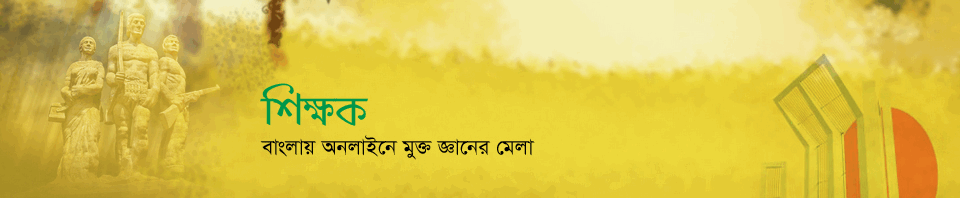লেকচার ভিডিওঃ
পদার্থবিজ্ঞান কি?

পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যা ভৌত জগতের সবকিছু নিয়েই আলোচনা করে। বিজ্ঞানের সবচেয়ে পুরানো এবং মৌলিক শাখা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমানু থেকে শুরু করে একেবারে পুরো মহাবিশ্ব,গ্যালাক্সির সবকিছুই আসলে পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। পদার্থের গঠন, প্রকৃতি, গতিবিধি,শক্তি বিশদভাবে এই সবকিছু এবং প্রাকৃতিক ও বস্তুগত ঘটনাগুলো পরস্পর কিভাবে সম্পর্কযুক্ত,কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এই ঘটনাগুলো ঘটে এই ব্যাপারগুলো নিয়েই পদার্থবিজ্ঞানীরা কাজ করেন। এভাবে কাজ করতে গিয়ে তাদের আবিষ্কৃত অনেক ধারনা, তত্ত্ব, সুত্র ব্যবহার করে অনেক কিছুই তৈরি করা হয় যা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনকে সহজ করে তোলে। পদার্থবিজ্ঞানী সহ সকল বিজ্ঞানীরাই কৌতুহলী মানুষ। তারা আমাদের চারপাশের ঘটনাগুলোর দিকে প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকান। তাদের এই কৌতুহলী দৃষ্টিই চারপাশের প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে এবং এর কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে তাদেরকে উৎসাহিত করে তোলে। বেশিরভাগ সময়ই কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে আরো অনেক প্রশ্ন সামনে চলে আসে। আর এই একের পর সামনে চলে আসা প্রশ্নই বৈজ্ঞানিক গবেষনা, পর্যবেক্ষন, পরীক্ষা এসব এগিয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় এক দল বিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ ফলাফল অন্য কোনো গবেষণা দলের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তাদের গবেষণার কাজে লাগে। আবার বিভিন্ন গবেষনার ফলাফল বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি পণ্য তৈরিতে অবদান রাখে। আর উন্নততর প্রযুক্তি আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তোলে। যুগে যুগে,শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে অসংখ্য ছোট-বড় বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে আমাদের আজকের সভ্যতা।
বিজ্ঞানের কোনো জাতীয় বা রাজনৈতিক সীমা নেই। বিজ্ঞানের উন্নতি,সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সকল জাতির সকল মানুষের জন্য। পদার্থবিজ্ঞানের প্রয়োগ প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ থেকে সহজতর করে তুলছে। শুধুমাত্র প্রযুক্তিকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারার জন্য হলেও আমাদের অল্পবিস্তর বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।
পদার্থবিজ্ঞান জানা একজন ব্যাক্তি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও খুব সহজেই কাজ করতে পারে। অনেকেরই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশুনার প্রতি একধরনের মোহ আছে। ইঞ্জিনিয়ার হলে চাকরি পেতে সুবিধা হয়, এটাই হয়ত এই মোহের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা আসলে পদার্থবিজ্ঞানকেই কৌশলে ব্যবহার করেন, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করেন। পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রকৃতির নিয়মগুলো বের করেন আর ইঞ্জিনিয়াররা সেই জ্ঞান ব্যবহার করে আমাদের জীবন সহজ করেন। কাজেই পদার্থবিজ্ঞানীদের কাজটাই কিন্তু আগে।
পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা
বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞান অনেক অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত এবং দিন দিন এই শাখা-প্রশাখা বাড়ছে। অথচ এক বা দুই শতাব্দীকাল আগেও বিজ্ঞানের এত শাখা-প্রশাখা ছিল না। ঐ সময়টাতে বিজ্ঞানের সাথে শিল্প-সাহিত্যের মত বিষয় একত্রে ছিল। ফলে পদার্থবিদ্যার উন্নতির প্রভাব এর সাথে জড়িত অন্য শাখাগুলোতেও পড়েছিল।
এরপর বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে। এর বিস্তৃতি বেড়েছে। এই ব্যাপকতার কারণেই বিজ্ঞানের আলোচনা, গবেষণা, পড়াশোনা এখন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ইত্যাদি শাখায় বিভক্ত। আর এই প্রতিটি শাখাই আবার অনেক উপশাখায় বিভক্ত। পদার্থবিজ্ঞানেও এমন বিস্তৃত অনেক শাখা আছে। স্কুলের শিক্ষার্থীরা হয়ত এখনই উচু পর্যায়ের পদার্থবিজ্ঞানের শাখাগুলোর আলোচনার বিষয় ভালভাবে বুঝতে পারবে না। প্রাথমিকভাবে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে আমরা যেটুকু ফিজিক্স পড়ব সেটাকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারিঃ বলবিদ্যা(Mechanics), তাপবিজ্ঞান(Thermodynamics), তরংগ ও শব্দ(Wave and Sound), আলো(Light), তড়িৎ ও চৌম্বক (Electricity and Magnetism), আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও ইলেক্ট্রনিক্স (Modern Physics and Electronics)। নাম শুনেই মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে এই আলাদা আলাদা ভাগে আমরা আসলে কি কি পড়ব। পড়তে গেলেই আমরা বিস্তারিত ভাবে জানব আমরা আসলে কোন অংশে কি পড়ছি। এই লেখাতে পদার্থবিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা বোঝানোর জন্য একজন স্কুলের বা কলেজের শিক্ষার্থী তার বইতে পদার্থবিজ্ঞানের যে বিষয়গুলো পড়ে সেগুলোকেই আমরা বিভিন্নভাগে ভাগ করতে পারি। এখানে আমরা মূলত তোমাদের মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বই অনুসারে বিভাজন করেছি। চাইলে তোমরা তোমাদের বইয়ের সাথে মিলিয়ে নিতে পার।
বলবিদ্যা বা Mechanics অংশে গতি সম্পর্কিত বিষয়াদি, বল, বল সম্পর্কিত নিউটনের সূত্র, কাজ, ক্ষমতা, শক্তি, চাপের বিষয়াদি, স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি পড়ানো হয়।

বিভিন্ন রকম গতি, বল, শক্তি এবং এ সম্পর্কিত বিষয় মেকানিক্সের আলোচ্য বিষয়
বস্তুর উপর তাপের প্রভাব, তাপ প্রয়োগের ফলে বস্তুর প্রসারণ, পদার্থের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন, তাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন স্কেল, এদের মধ্যে সম্পর্ক, তাপ সঞ্চালণের বিভিন্ন পদ্ধতি, বিভিন্ন তাপীয় যন্ত্র, এসবের বর্ণনা ইত্যাদি তাপবিজ্ঞান(Thermodynamics) আলোচ্য বিষয়।

বস্তুর উপর তাপের প্রভাব ও তাপ সম্পর্কিত বিষয়াদি তাপবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়
তরংগ ও শব্দ (Wave and Sound) অংশে তরংগ এবং শব্দ সম্পর্কে পড়ানো হয়। তরংগ কি? কিভাবে তরংগ সৃষ্টি হয়? কিভাবে একটা মাধ্যমে তরংগ প্রবাহিত হয়? তরংগের মাধ্যমে শক্তির প্রবাহ, তরংগের বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন প্রকার তরংগ, তরংগের উপরিপাতন, বিভিন্ন মাধ্যমে তরংগের বেগের ভিন্নতা, শব্দ তরংগ, শব্দ কিভাবে আমাদের কানে এসে পৌঁছে, কিভাবে আমরা শব্দ শুনতে পাই এসব আমরা এই অংশে পড়ব।

পানিতে সৃষ্টি হওয়া তরংগ
এরপর আসছে আলো ও এর বিভিন্ন দিক। আলো কি? আলোর বিভিন্ন ধর্ম, আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিভিন্ন রকম লেন্স, বিভিন্ন রকম আয়না, ডিফ্রেকশন, ইন্টারফেরেন্স, পোলারাইজেশন, প্রিজমে আলোর বিচ্ছুরণ, বিভিন্ন আলোকযন্ত্র ইত্যাদি এই অংশের আলোচ্য বিষয়।


উত্তল লেন্স

আলোর প্রতিফলন
তড়িৎ অধ্যায়ের পড়াশুনা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। স্থির তড়িৎ ও চল তড়িৎ।
স্থির তড়িৎ এর মধ্যে আছে তড়িৎ চার্জ, তড়িৎ বল, তড়িৎ আবেশ, কুলম্বের সূত্র, তড়িৎ ক্ষেত্র, তড়িৎ বিভব, বিভব পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা।


পজিটিভ পয়েন্ট চার্জ (ধনাত্মক বিন্দু আধান)

তড়িৎ বীক্ষণ যন্ত্র
চল তড়িৎ এর মধ্যে আছে তড়িৎ কোষ, ব্যাটারি, তড়িৎ বর্তনী, সমান্তরাল সংযোগ, অনুক্রমিক সংযোগ, ও’মের সূত্র, তড়িচ্চালক শক্তি, তড়িৎ প্রবাহিতা, রোধ, রোধের সূত্র, রোধের বিভিন্ন সন্নিবেশঃ সমান্তরাল সন্নিবেশ, অনুক্রমিক সন্নিবেশ ইত্যাদি।

তড়িৎ বর্তনী
পরবর্তী বিষয় চৌম্বকত্ব ও চুম্বক ধর্ম। চুম্বক, চৌম্বকত্ব, চৌম্বক বল, চৌম্বক বলরেখা, চৌম্বক ক্ষেত্র, স্থায়ী চুম্বক-অস্থায়ী চুম্বক, চুম্বকের আণুবীক্ষণিক চিত্র ইত্যাদি চুম্বক অংশের বিষয়। এরপর আমরা পড়ব তড়িৎ চৌম্বকত্ব। তড়িৎ প্রবাহের ফলে সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র, সলিনয়েড, তাড়িতচুম্বক ক্ষেত্র, তাড়িতচৌম্বক আবেশ, মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কার, তড়িৎবাহী তারের উপর চুম্বকের প্রভাব, বৈদ্যুতিক মোটর, জেনারেটর, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি এখানে আলোচনা করা হবে।

চুম্বক ও চুম্বক বলরেখা

U আকৃতির চুম্বক

তড়িত প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া

বৈদ্যুতিক মোটর
তড়িৎ, চুম্বক, তাড়িতচৌম্বক এসব পড়তে পড়তেই আমরা বুঝে যাব যে আমরা আস্তে আস্তে আধুনিক পদার্থবিদ্যার দিকে এগুচ্ছি। এতদুর পর্যন্ত আমরা যা পড়ব সেটা হচ্ছে ১৯০০ সালের আগে পর্যন্ত আবিষ্কৃত হওয়া ফিজিক্স। যাকে কিনা বলা হয় ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স (Classical Physics). এর পরবর্তী সময়ে পদার্থবিজ্ঞান এগিয়েছে আগের চেয়েও দ্রুত গতিতে। স্কুল-কলেজ পর্যায়ে আধুনিক পদার্থবিদ্যা অংশে আমরা পড়ব অণু-পরমানু, মৌলিক কণিকা ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন, এক্সরে, নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রাথমিক কিছু বিষয়, আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি। তবে আধুনিক পদার্থবিদ্যার আলোচনা অনেক অনেক বিস্তৃত। আসলে এই অংশের পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশুনা বুঝতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে সিরিয়াস পড়াশুনা করা লাগবে।

আধুনিক পদার্থবিদ্যা
রিলেটিভিস্টিক মেকানিক্স মূলত থিওরী অফ রিলেটিভিটির পড়াশুনা। মহা প্রতিভাধর পদার্থবিজ্ঞানী এলবার্ট আইনস্টাইনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ থিওরী অফ রিলেটিভিটির জন্য। এটা তাঁর থিওরী। আইনস্টাইন, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ !!!
কোয়ান্টাম ফিজিক্সের শুরু এবং বিকাশ এই আধুনিক পদার্থবিদ্যার উল্লেখযোগ্য এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শ্রোডিঞ্জার, হাইজেনবার্গ, পল ডিরাক… এই নামগুলো কোয়ান্টাম মেকানিক্সে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিতর্ক থাকতে পারে কোয়ান্টাম থিওরী স্কুলের শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝবে সেটা নিয়ে। কিন্তু বিস্তারিত পড়া শুরু না করলেও অন্তত এই কোয়ান্টাম জগতে উঁকি দিয়ে একটু দেখা যেতেই পারে। এখন অনেক উন্নত দেশের স্কুলের টেক্সট বইতেই শেষের দিকে করে কোয়ান্টাম থিওরী নিয়ে শিক্ষার্থীদের সহজ করে কিছুটা ধারনা দেয়া হয়। আসলে এখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্স তেমন একটা পড়ানো হয় না, শুধু এটা বোঝানো হয় কেন কোয়ান্টাম মেকানিক্স জরুরি, পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে কিভাবে এর শুরু। কোয়ান্টাম মেকানিক্স মূলত অণু-পরমাণুর ক্ষুদ্র জগতকে ব্যাখ্যা করে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে পদার্থবিজ্ঞান দেখে অভ্যস্ত, আমাদের চারপাশে যে পদার্থবিজ্ঞান প্রয়োগ করে আমরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করি, অণু-পরমানুর অতি ক্ষুদ্র জগতে সেই পদার্থবিজ্ঞান খাটানো যায় না। সেখানে ব্যবহার করতে হয় কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এটা আধুনিক পদার্থবিদ্যারই অংশ।
যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শুরু হবে তখন পদার্থবিজ্ঞানের আরো অনেক শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে তোমাদের আরো ধারনা হবে। আগ্রহীদের জন্য এখানে উইকিপিডিয়া থেকে Branches of Physics পাতাটার লিঙ্ক যুক্ত করে দেয়া হল।
পদার্থবিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা নিয়ে যদি আরো জানতে চাও তাহলে এই লিংকে গিয়ে দেখতে পার।
পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশুনা
পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশুনা একটা জীবনব্যাপী সাধনা। এই পড়াশুনা কখনোই শেষ হয় না। ফিজিক্সের পড়াশুনাটা কেবল কিছু ফর্মুলা বা সংজ্ঞা জানা বা মুখস্থ করা না। অনেক ছাত্র-ছাত্রীই মনে করে কিছু ফিজিক্সের কিছু সূত্র/ফর্মুলা মুখস্থ করে ঐ ফর্মুলা গুলোতে কিছু সংখ্যা বসিয়ে অংকের উত্তর মেলানোই ফিজিক্সের পড়াশুনা। সূত্র মুখস্থ করে ফিজিক্সের অংক মিলানো আর সত্যিকার ভাবে পদার্থ বিজ্ঞান বোঝার মধ্যে তফাৎ আছে। আমাদের পদার্থ বিজ্ঞানের ধারণা, নীতি গুলো আগে বুঝতে হবে ভালমত। এবং সেগুলো বুঝে নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পদা্থবিজ্ঞানের সেই নীতি/সূত্র গুলোর ব্যবহার কিভাবে হয় সেটা ভালমত জানতে হবে।
একটা উদাহরণ দেই। আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল (A) = দৈর্ঘ্য (L) × প্রস্থ (h)
A=Lh
এখন কোনো একজন শিক্ষার্থীকে যদি বলা হয় যে
আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, L = ৫ মিটার ,
প্রস্থ, h = ২ মিটার।
এর ক্ষেত্রফল বের কর। খুব সহজেই সে এটা বের করে ফেলতে পারবে।
ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ = ৫ মিটার × ২ মিটার = ১০ মিটার২
এখন একই প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে করি। একটা আয়ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ২৪ মিটার২ । বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের এবং প্রস্থের আয়তক্ষেত্র ডিজাইন কর যাদের প্রত্যকের ক্ষেত্রফল ২৪ মিটার২ । দেখা যাবে অনেকেই এই সমস্যাটার সমাধান আর করতে পারছে না।
পূর্ণ সংখ্যা ব্যবহার করে বেশ কয়েকভাবেই ডিজাইন করা যায়।
১২×২ = ২৪
৬×৪ = ২৪
৮×৩ = ২৪
২৪×১ = ২৪
আর যদি ভগ্নাংশ দৈর্ঘ্যের এবং প্রস্থের আয়তক্ষেত্র বানাতে চাই তাহলে অসংখ্য আয়তক্ষেত্র নেয়া যাবে যাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রফল ২৪ মিটার২।
যখন আমরা ফিজিক্স শিখব তখন আমাদের শুধু নীতি-সূত্র মুখস্থ করার চেয়ে বার বার চিন্তা করে সেগুলো বিভিন্ন রকম সমস্যায় ব্যবহার করে গোটা বিষয়টা আত্মস্থ করার দিকে বেশী মনযোগী হতে হবে। অর্জন করা জ্ঞান দিয়ে অনেক অনেক বাস্তব সমস্যা সমাধান করতে জানতে হবে। সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে যে যত বেশি সক্রিয় হবে সে তত বেশি শিখবে। যখন কোনো পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবে তখন নিছক রিভিশান দেবার বদলে একটু অন্যভাবে পড়তে পার। আগে পড়া বিষয়টা বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতে পার, নতুন নতুন সমস্যা সমাধান করতে পার যেগুলা প্রথম বার পড়ার ক্ষেত্রে করনি।
তবে শুধু পরীক্ষার প্রস্তুতি ছাড়াও পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশুনা একটা রোমাঞ্চকর অভিযানের মত। আর এই রোমাঞ্চকর অভিযান কখনো শেষ হয় না, চলতেই থাকে। একটা চ্যালেঞ্জ পার হলে পরবর্তী চ্যালেঞ্জ সব সময় তৈরি থাকে। এটাই ফিজিক্সের মজা। এটা পুরোপুরি আমাদের উপর নির্ভর করে কিভাবে আমরা এই চ্যালেঞ্জগুলোকে নিচ্ছি, কিভাবে এদের মোকাবেলা করছি। কখনো কখনো হয়ত আমরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকি না। প্রস্তুতির অভাবে তাই পেরেও উঠি না। তাছাড়া যেকোনো চ্যালেঞ্জ পার হবার জন্য কিছু ধৈর্য্য, চেষ্টা, অধ্যাবসায়, খানিকটা মেধা এসব গুণাবলীও থাকা লাগে। এগুলো কমবেশী আমাদের সবারই আছে। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে পদার্থবিজ্ঞানের এই রোমাঞ্চকর অভিযানও অসহ্য ঠেকে অনেকের কাছে। কিন্তু ধৈর্য্য ধরে এগুলে, খাটুনিটা ঠিকঠাক মত করলে এটা কোনো ব্যাপারই না। খাটুনি নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এটা একটা রোমাঞ্চকর অভিযান। আর এই অভিযানের উপভোগের অংশ এটাই; বার বার চেষ্টা করে যাওয়া। সহজ ভাবে এবং ধৈর্য্য ধরে এগুলে সমস্যা সমাধানের আনন্দের কাছে এই কষ্টটা কিছুই না। একটা সত্যিকার কৌতুহলী মন তার কৌতুহল মেটানোর জন্য অনেকদুর যেতে পারে। পদার্থবিজ্ঞান শেখার ক্ষেত্রে আমাদের ঠিক সেই কাজটাই করতে হবে।
গণিতঃ পদার্থবিজ্ঞানের ভাষা

পদার্থবিজ্ঞানের ভাষা গণিত
পদার্থবিজ্ঞানের একটা অবাক করা দিক হল যে এর ফলাফলগুলো খুব অল্প কথার সূত্র, মূলনীতি, তত্ত্বের সাহায্যে প্রকাশ করে ফেলা যায়। এই তত্ত্ব-মূলনীতি সবসময় গাণিতিকভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। পদার্থবিজ্ঞানীরা যাই আবিষ্কার করেন না কেন, যে তত্বই দেন না কেন সবসময় তাঁরা এটা গাণিতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন।
গণিতের এমন কিছু শাখা আছে যেটা কিনা আবিষ্কারের সময় এর ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে বিজ্ঞানের কোনো একটা শাখার কোনো একটা গবেষণায় সেই গণিত কাজে লেগে গেছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা তত্ত্ব দেওয়া, তত্ত্বের সত্যতা যাচাইয়ের পরীক্ষা করা, পরীক্ষার মডেল ডিজাইন করা, পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করা এইসব কাজে সবসময় সংশ্লিষ্ট গণিতের উপর নির্ভর করেন। এক কথায় এভাবে বলা যায় গণিত হল পদার্থবিজ্ঞানের ভাষা। এবং এটা খুব শক্তিশালী ভাষা। ভালমত ফিজিক্স বুঝতে হলে ফিজিক্সের ভাষা গণিত ভাল জানতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা হয় সেটা হল আমরা গণিতের কোনো একটা অংশে এসে আটকে যাই। গাণিতিক প্রতীক-সমীকরণ এসব দেখে পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশুনায় পিছিয়ে যাই। আসলে যা হয় সেটা হল পদার্থবিজ্ঞানের ঐ অংশটা যে গাণিতিক ভাষায় লেখা হয়েছে সেই গণিতটা আমরা ঠিক মত জানি না। বিভিন্ন গাণিতিক সমীকরণ, ক্যালকুলেশান ইত্যাদির সাহায্যে পদার্থবিজ্ঞানের নীতিগুলো কিভাবে প্রকাশ করা হয়েছে সেটা বোঝা পদার্থবিজ্ঞান পড়াশুনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ভালমত গণিত জানাটা পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশুনা অনেক সহজ করে দেয়। যতই আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশুনা এগুবে দেখবে ততই আমাদের নতুন নতুন পদ্ধতির গণিত জানতে হচ্ছে।