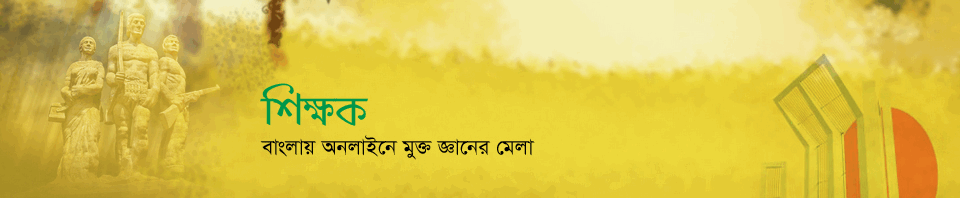[কোর্সের মূল পাতা | নিবন্ধনের লিংক]
নিউরোবিজ্ঞানের সরল পাঠ লেকচার সিরিজের লেকচার ৪
Neurotransmitter from Mamoon Rashid on Vimeo.
Link: http://vimeo.com/58608044
নিউরোট্রান্সমিটার
এক কথায় নিউরোট্রান্সমিটারসমূহ হলো বিশেষ কিছু অণু যারা নার্ভের প্রান্ত থেকে নি:সরিত হয়ে অপর নিউরন বা গ্রন্থির দ্বারা গৃহীত হবার মাধ্যমে আন্ত:নিউরনীয় তথ্য পরিবহনের কাজ করে থাকে। এদের আণবিক গঠন সাধারণত: খুব একটা বড় হয় না, এবং এরা খুব দ্রুত তাদের কাজ সেরে ফেলার পর হয় নিষ্ক্রিয় হয় অথবা পুনরায় নিউরন কর্তৃক গৃহীত হয়।
সাইন্যাপ্স এর সাধারণ কাঠামো
নিউরন কিভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য আমি সংক্ষেপে সাইন্যাপসের কাঠামো আলোচনা করেছি।
অ্যাসিটাইল কোলিন (অ্যা.কো.)
অ্যা.কো. হলো সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত নিউরোট্রান্সমিটার, যা আজ থেকে প্রায় পৌনে এক শত বছর আগে আবিষ্কৃত হয়। এই নিউরোট্রান্সমিটারটি নি:সরিত হয় যেসব নিউরন ঐচ্ছিক পেশীর সাথে সংযুক্ত থাকে এবং যারা হার্টবিট নিয়ন্ত্রন করে, সেইসব নিউরনের প্রান্ত থেকে। এছাড়া অ্যা.কো. ব্রেইনের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যকার তথ্যবাহী নিউরোট্রান্সমিটার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।
কীভাবে অ্যা.কো. নি:সরিত হয় ও কাজ করে?
নার্ভের অ্যাক্সন এর প্রান্তদেশে অ্যা.কো. তৈরী হয় ও থলি বা “ভেসিকল” এর মধ্যে মজুদ থাকে। যখন কোন অ্যাকশন পটেনশিয়াল ওই অ্যাক্সনের প্রান্তদেশে এসে পৌছায়, তখন ক্যালসিয়াম আয়ন উক্ত প্রান্তের ভেতরে প্রবেশ করে এবং থলের মধ্যে থাকা অ্যা.কো. নি:সরিত হয়। নি:সরণের পরে অ্যা.কো. সাইন্যাপটিক ফাঁকা জায়গা অতিক্রম করে পরবর্র্তী কোষের মেমব্রেনের উপরের নির্দিষ্ট অ্যা.কো. রিসেপ্টরের সাথে সংযুক্ত হয়। এই পরবর্তী কোষটি যদি ঐচ্ছিক পেশী হয় তাহলে রিসেপ্টরের সাথে অ্যা.কো. বাইন্ড করার ফলে সোডিয়াম চ্যানেল খুলে যায় ও বাইরে থেকে কোষের ভেতরে প্রচূর পরিমান সোডিয়ামের প্রবেশ ঘটে এবং এর ফলশ্রুতিতে এক পর্যায়ে গিয়ে পেশীর সংকোচন ঘটে।
প্রসঙ্গ অ্যাসিটাইলকোলিনএস্টারেজ:
‘অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ’ নামের একটি এনজাইম অ্যা.কো. কে ভেঙে অকার্যকর করে দেয়, যাতে অনাকাংক্ষিত পরিমাণ লম্বা সময় ধরে অ্যা.কো. তার রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকতে না পারে।
যদি কোন কারণে অ্যা.কো. তার রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করতে না পারে, তাহলে পেশীর সংকোচন ঘটবে না। যেমন ধরুন, মায়েস্থেনিয়া গ্র্যাভিস নামের একটা অসুখের কথা, যেখানে অ্যা.কো. এর এক ধরণের রিসেপ্টর অ্যান্টিবডির দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে থাকে, ফলে অ্যা.কো. সেখানে বসে তার কাজ করতে পারে না। ফলে, রোগীর সব সময় দূর্বল বোধ হয় ও ক্লান্ত লাগে।
ব্রেইনের মধ্যে অ্যা.কো. কী কাজ করে সে বিষয়টা নিয়ে খুব বেশী তথ্য আমাদের জানা নেই। ধারণা করা হয় যে, মনোযোগ, স্মৃতি ও ঘুম সংঘটনে অ্যা.কো. এর ভূমিকা আছে। অ্যালঝেইমার এর রোগীদের ক্ষেত্রে অ্যা.কো. নি:সরণকারী নিউরনের মৃত্যু ঘটে বলে বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্র হলো এই নিউরণের উপর গবেষণা করে অ্যালঝেইমার এর চিকিৎসা বের করা।
পরবর্তী ধরণের নিউরোট্রান্সমিটার: অ্যামাইনো এসিড সমূহ (এ.এ.)
ব্রেইন সহ আমাদের সারা দেহের সমস্ত প্রোটিনের বিল্ডিং ব্লক বা গঠনগত একক হলো এমাইনো এসিড। মজার ব্যাপার হলো, ব্রেইনের মধ্যে কিছু এমাইনো এসিড নিউরোট্রান্সমিটারের ভূমিকা পালন করতে পারে।
গামা এমিনো বিউটাইরিক এসিডকে সংক্ষেপে গাবা নামে ডাকা হয়। গ্লাইসিন হলো সবচেয়ে ছোট এমিনো এসিড। গ্লাইসিন এবং গাবা এই দুই এমিনো এসিড নিউরনের ফায়ারিং বা উত্তেজিত হয়ে ওঠার বিষয়টাকে দমন করে। এ কারণে এ ধরণের নিউরোট্রান্সমিটারকে বলে ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার, যার বাংলা নাম আমি দিয়েছি “প্রশমক” নিউরোট্রান্সমিটার। ঘুমের ওষুধ (যেমন বেনজো ডায়াজিপাইনস গ্রুপ) এবং খিঁচুনির ওষুধ হিসাবে যে ওষুধ গুলো ব্যবহার করা হয় তারা ব্রেইনের মধ্যে গাবা-এর কার্যক্রম বাড়িয়ে দেয়।
হানটিংটন ডিজিজ নামের এক ধরণের বংশগত অসুখ আছে, যা সাধারণত: মাঝ বয়েসের পরে রোগীর মধ্যে প্রকাশ পায়। রোগীর চলাফেরা ও হাত পা নাড়াচাড়া করার মধ্যে ছন্দবদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রনের অভাব থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ব্রেইনের যে অংশটি আমাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে সেই অংশের গাবা-উৎপাদনকারী নিউরনগুলোর মৃত্যুর কারণে এই রোগের উদ্ভব হয়।
গ্লুটামিক এসিড (যাকে আয়ন বিবেচনা করে সংক্ষেপে গ্লুটামেট বলে) এবং অ্যাসপারটেট হচ্ছে ব্রেইনের এক্সাইটেটরি বা উত্তেজক নিউরোট্রান্সমিটার। এন-মিথাইল ডি-অ্যাসপারটেট বা সংক্ষেপে এনএমডিএ রিসেপ্টর এর সাথে গ্লুটামিক এসিড যুক্ত হয়ে কোষের মধ্যে যে কার্যকলাপ সংঘটিত করে তার একই সাথে ভালো এবং খারাপ প্রভাব রয়েছে। এনএমডিএ রিসেপ্টর যেমন আমাদের শিক্ষণ ও স্মৃতিধারণে ভূমিকা রাখে, ঠিক একই ভাবে এই রিসেপ্টরের অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হবার কারণে নিউরনের ক্ষতি বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, যার ফলে রোগী ব্রেইন স্ট্রোকের শিকার হতে পারেন।
মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যায় হচ্ছে স্ট্রোকের প্রতিষেধক গবেষণা করে বের করার পেছনে। স্ট্রোক-বিজ্ঞানীদের বিশেষ কৌতুহলের বিষয় হলো এই এনএমডিএ রিসেপ্টর, বিশেষত: এর কাঠামো, কিভাবে এটি নিয়ন্ত্রি হয়, এর অবস্থান এবং সর্বোপরি কাজ। ব্রেইন কীভাবে কাজ করে তা ভালো করে বোঝার জন্য এবং নিউরোলজিক্যাল ও মানসিক বিভিন্ন অসুখের চিকিৎসার জন্য এনএমডিএ রিসেপ্টর সম্পর্কে গবেষণা প্রয়োজন।
অ্যামাইনো এসিডের পরে এবার আমরা ক্যাটেকোলামিনস ধরণের অণু নিয়ে কথা বলবো
আমাদের ব্রেইন এবং প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রচূর পরিমাণে ডোপামিন এবং নরেপিনেফ্রিন উপস্থিত রয়েছে। ব্রেইনের তিনটি প্রধান সার্কিটের মধ্যে ডোপামিন উপস্থিত থাকে, এই সার্কিটগুলো আমাদের চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রন করে, মনোরোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি করে এবং হরমোনের প্রতিক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।
আমাদের চলৎশক্তি বা চলাচল করার বিষয়টার সাথে জড়িয়ে আছে ডোপামিনের যে সার্কিটটি, তার সাথে পারকিনসন্স ডিজিজের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। ব্রেইনে ডোপামিনের ঘাটতি হলে পেশীতে খিঁচুনি, পেশী শক্ত হয়ে যাওয়া এবং হাঁটাচলায় অসুবিধা এসব সমস্যা দেখা দেয়। লেভোডোপা হলো একটি রাসায়নিক পদার্থ যার থেকে ডোপামিন উৎপন্ন হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, পারকিনসন্স ডিজিজের রোগীদের জন্য লেভোডোপা প্রয়োগ করলে তাদের হাঁটাচলা ও যেসব কাজে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয় সেগুলো তারা বেশ ভালো ভাবেই করতে পারেন।
ডোপামিনের আরেকটি সার্কিট আছে যাকে অনুধাবন ও আবেগীয় কর্মকাণ্ডর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই সার্কিটটির অস্বাভাবিকতার সাথে সিজোফ্রেনিয়া নামক অসুখের সম্পর্ক রয়েছে। কিছু ড্রাগ আছে যারা ব্রেইনের নির্দিষ্ট ডোপামিন রিসেপ্টরকে ব্লক করে দেয় এবং রোগীদের আবেগীয় অস্বাভাবিকতার উপশম করতে পারে। এ কারণে মানসিক রোগ সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে আমাদের এই নিউরোট্রান্সমিটার সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে।
ডোপামিনের তৃতীয় সার্কিটটি হলো এন্ডেক্রিন বা হরমোন নি:সরণ সিস্টেম। ডোপামিনের নির্দেশে হাইপোথ্যালামাস হরমোন তৈরী করে এবং সেগুলোকে পিটুইটারি গ্রন্থির মধ্যে জমা করে রাখে, যেখান থেকে পরবর্তীতে দরকার মতো রক্ত স্রোতে সেই হরমোনকে নি:সরিত করা হয়।
নরেপিনেফ্রিনবাহী নার্ভতন্তুসমূহ আমাদের সমস্ত ব্রেইন জুড়েই উপস্থিত। এই নিউরোট্রান্সমিটারের ঘাটতির ফলে অ্যালঝেইমারস, পারকিনসন্স ডিজিজ এবং কোরসাকফ’স সিনড্রোম নামের অসুখের উদ্ভব ঘটে।
আগের আলোচনায় বলেছিলাম, আমাদের সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম কর্তৃক নরেপিনেফ্রিন নি:সরিত হয়, যা তাৎক্ষণিক ভাবে আমাদের হার্টের গতি ও রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়।
পরের লেকচারে আরো কিছু ক্যাটাগরির নিউরোট্রান্সমিটার নিয়ে কথা হবে।