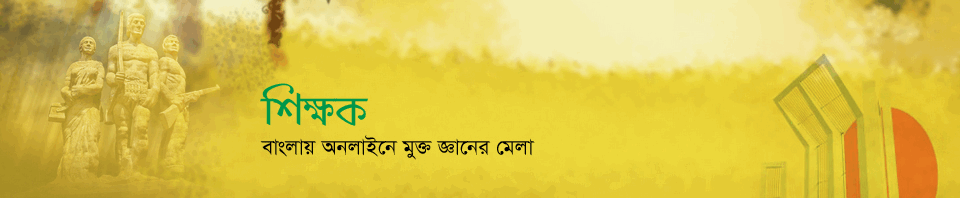কোর্স পরিচিতি ও নিবন্ধনের ফর্ম।
আপডেট: ইউটিউবে দেখতে না পেলে লেকচারের ভিডিও আছে এখানেও।
আজকে আমরা ও’মের সূত্র ও এলিমেন্টদের অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে আলোচনা করবো।
একটা সার্কিটের মধ্যে দিয়ে কি পরিমান কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তা তড়িৎপ্রকৌশলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারেন্ট যখন তারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন সেই শক্তির কিছুটা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই কারণে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে তারের পরিধি নির্ধারণ করা হয়। এর সাথে সাথে যদি সার্কটে সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে যন্ত্রপাতিকে ড্যামেজ থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রটেকশন ডিভাইসও ব্যবহার করা হয় যেগুলোকে সিলেক্ট করা হয় সার্কিটে নরমাল অবস্থায় কি পরিমান কারেন্ট প্রবাহিত হয় তার উপর নির্ভর করে।
স্লাইড এর পিডিএফ
স্ক্রিপ্ট এর পিডিএফ
তাহলে, প্রশ্ন হচ্ছে একটা সার্কিটে কি পরিমান কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তা আমরা নির্ণয় করবো কিভাবে?
প্রাথমিক ভাবে আমাদের প্রথম হাতিয়ার হবে ও’মের সূত্র। ও’মের সূত্র মতে একটা রেসিস্টর দিয়ে গঠিত সার্কিটে যদি V পরিমাণ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয় R পরিমাণ রেসিসটেন্স এর দুই পাশে, তাহলে সার্কিটে যে I পরিমান কারেন্ট প্রবাহিত হবে, তা নিম্নের সূত্র মেনে চলবে –
ও’মের সূত্র:
V = IR
কেবলই গাণিতিক ভাবে চিন্তা করলে, এই সূত্র আমাদের কি বলছে?
- ধ্রুবক রেসিসটেন্স এর জন্যে, ভোল্টেজ কমালে কারেন্ট কম প্রবাহিত হবে, আর ভোল্টেজ বাড়ালে কারেন্ট বেশি প্রবাহিত হবে।
- ধ্রুবক ভোল্টেজের জন্যে, রেসিসটেন্স বেশি হলে কারেন্ট কম প্রবাহিত হবে, আর রেসিসটেন্স কম হলে কারেন্ট বেশি প্রবাহিত হবে।
তাহলে ১০V ভোল্টেজের উৎসকে একটা ৫ Ω রেসিস্টেন্স (রোধ) এর সাথে যুক্ত করে বর্তনী সম্পন্ন করা হলে বর্তনীতে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে তা আমরা বের করবো এভাবে –
সূত্র থেকে, I = V/R = (১০V)/(৫ Ω) = ২ A
সার্কিট সিমুলেটর অ্যাপ্লেট এর লিংক – http://www.falstad.com/circuit/
তো উপরের উদাহরণে তো আমরা মাত্র একটা রেসিস্টর ব্যবহার করেছি। বাস্তবে কি সার্কিট এতটাই সহজ সরল হয়?
এর উত্তর হচ্ছে না। বাস্তবে একটা বিদ্যুত ব্যবহার করে আমরা যেগুলো চালাই – যেমন লাইট বাল্ব, সেগুলোকে “লোড” বলে। বেশির ভাগ “লোড”ই একেকটা রেসিসটর। এমনকি যে তার ব্যবহার করে লোড গুলিকে সার্কিটে যুক্ত করা হয়, তাও রেসিস্টর হিসেবে কাজ করে। যদিও আমরা এখনকার মতন হিসেবের সুবিধার্থে তারের রেসিসটেন্সকে অবহেলা করছি।
তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে জটিল সার্কিটে আমরা কিভাবে হিসাব নিকাশ করি?
আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে এলিমেন্টগুলি কিভাবে সংযুক্ত রয়েছে। সাধারণভাবে মূলত: দুইভাবে এদের সংযোগ করা যায় –
সিরিজ:
সিরিজ বর্তনী হলো একটা ট্রেনের মতন। প্রতিটা রেসিস্টরের এক প্রান্ত অন্যটার আরেক প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকবে।
১) প্রতিটি রেসিস্টরের মধ্যে দিয়ে একই (সমান পরিমাণ) কারেন্ট প্রবাহিত হবে।
২) প্রতিটি রেসিস্টরে ভোল্টেজ ড্রপ এর মান নির্ভর করবে প্রতিটি রেসিস্টরের
মানের উপরে।
৩) সিরিজে থাকা সবগুলো রেসিস্টরকে একটা রেসিস্টর দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে গেলে সেই রেসিস্টরের মান যা হবে তাই হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট বা মোট রেসিসটেন্স।
সূত্র:
Rtotal = R1+R2+…Rn
প্যারালাল:
প্যারালাল বর্তনী হলো একটা মই এর মতন। সবগুলো রেসিস্টর দুই প্রান্তেই অন্য সবগুলোর সাথে যুক্ত থাকবে।
১) প্রতিটি রেসিস্টরের দুপাশের ভোল্টেজ ড্রপ একই (সমান) হবে।
২) প্রতিটি রেসিস্টরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমান মান নির্ভর করবে প্রতিটি রেসিস্টরের মানের উপরে।
৩) প্যারালালে থাকা সবগুলো রেসিস্টরকে একটা রেসিস্টর দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে গেলে সেই রেসিস্টরের মান যা হবে তাই হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট বা মোট রেসিসটেন্স।
সূত্র:
(1/Rtotal) = (1/R1) + (1/R2) + … + (1/Rn)
কুইজ – ২ কুইজে অংশ নিতে হলে এখানে ক্লিক করুন অথবা নিচের ফর্মে সরাসরি কুইজটির জবাব দিন।