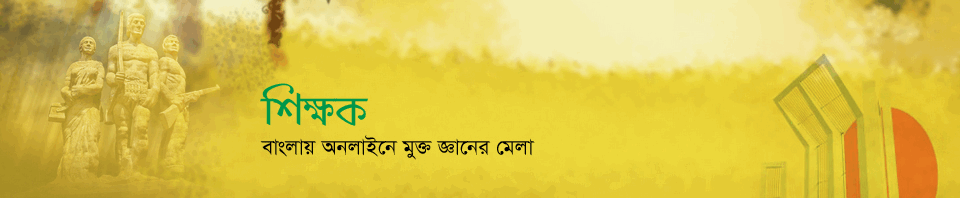[কোর্সের মূল পাতা | নিবন্ধনের লিংক]
নিউরোবিজ্ঞানের সরল পাঠ লেকচার সিরিজের লেকচার ২
এক নজরে ব্রেইন ও নার্ভাস সিস্টেম
ভিডিও লিংক: ইউটিউব:
ভিমিউ ভিডিও লিংক:
https://vimeo.com/50189149?action=share
ব্রেইনের রয়েছে বিভিন্ন কাঠামোগতভাবে স্বতন্ত্র অঞ্চল এবং তাদের মধ্যে যোগসূত্র।
ব্রেইনের বিভিন্ন অঞ্চল:
সেরেব্রাম:
ব্রেইনের সবচেয়ে বড় অংশ। আমাদের সব ঐচ্ছিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রনে ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করা, অনুধাবন করা, পরিকল্পনা এবং ভাষা বুঝতে পারা এগুলোর সবই নিয়ন্ত্রিত হয় সেরেব্রাম অঞ্চলের দ্বারা। সেরেব্রামের দুইটি খন্ড আছে, যাদেরকে অর্ধগোলক এর সাথে তুলনা করা চলে। এরা মাথার বাম ও ডান এই দুই পাশে অবস্থিত। একগুচ্ছ তন্তু বা সুতোর মত কাঠামোওয়ালা টিসু এই দুই অর্ধগোলকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে, যার নাম করপাস ক্যালোসাম।
সেরেব্রাল করটেক্স হলো সেরেব্রাম এর একদম বাইরের পাতলা আবরণ। এর রং যেহেতু গ্রে বা ধূসর, সেরেব্রাল করটেক্স কে অনেক সময় গ্রে ম্যাটারও বলা হয়। আমরা যখন ব্রেইনকে দেখি তখন প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে ব্রেইনের বাইরের পিঠে অসংখ্য ভাঁজ। অল্প জায়গার মধ্যে যদি অনেক বড় কোন শীট বা কাগজ রাখতে হয় তাহলে অবশ্যই ওই শীটটাকে উঁচু নীচু অবস্থায় বা ভাঁজ করে রাখতে হবে। আমাদের ব্রেইনে যে এত ভাঁজ, তার প্রধান কারণ আমাদের করটেক্স এর ক্ষেত্রফল অন্য প্রাণীর তুলনায় (যেমন বানর, শিম্পাঞ্জি) অনেক বেশি। কর্টেক্সের মোট ক্ষেত্রফলের দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি অঞ্চল ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে ঢুকে থাকে।
সামগ্রিক ভাবে সেরেব্রাল কর্টেক্স কি কাজ করে সেটা তাদের বিভিন্ন অংশ বা অঞ্চল দ্বারা নির্ধারিত হয়।
সামনের খণ্ড বা ফ্রন্টাল লোব:
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়ার (যাকে বলে মোটর মুভমেন্ট) সিদ্ধান্ত ও নিয়ন্ত্রণ আসে সামনের খণ্ড থেকে। উদাহরণ স্বরূপ, হ্যান্ডশেক করার সময় হাত বাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ আসে এখান থেকে। এছাড়া উচ্চতর চিন্তন প্রক্রিয়া (অঙ্ক সমাধান করা), চিন্তা, পরিকল্পনা, সমন্বয়করণ, ব্যক্তিত্ব ও আবেগীয় বৈশিষ্ট ইত্যাদির নিয়ন্ত্রন হয় এখান থেকে।
প্যারাইটাল লোব:
ব্রেইনের এই অংশটি অনুভূতি প্রক্রিয়াকরণ (সেনসরি প্রসেসিং), মনোযোগ ও ভাষা ব্যবহারের সাথে জড়িত। প্যারাইটাল লোবের ডান অংশ যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে ত্রিমাত্রিক অবস্থানের সাপেক্ষে নিজের অবস্থান বুঝতে ও সমন্বয় করতে অসুবিধা হয়। আবার, যদি বাম অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে লিখিত বা পঠিত ভাষা বুঝতে অসুবিধা হয়।
অক্সিপিটাল লোব:
এটা দৃষ্টির ব্যাপারটা প্রসেস করে এবং বস্তুর আকৃতি ও রং সম্পর্কে আমাদের বুঝতে সাহায্য করে।
টেমপোরাল লোব:
শ্রবণ এর মাধ্যমে অনুভূত তথ্যকে প্রসেসিং করে এই অংশ। এ ছাড়া অন্যান্য অনুভূতিগুলোকে এক সাথে সমন্বয় করতেও সহায়তা করে এটি। ব্রেইনের মধ্যে হিপোক্যাম্পাস নামে ছোট একটি অংশ আছে এই লোবের কাছে, যার দ্বারা শর্ট টার্ম মেমোরি বা স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি প্রসেসিং করা হয়।
মোটামুটি উপরে উল্লেখিত এগুলো নিয়েই ফোরব্রেইন বা সম্মুখ ব্রেইন গঠিত হয়। ফোরব্রেইনের আরো কয়েকটি অংশ হলো, ব্যাসাল গ্যাংগ্লিয়া যা হলো সেরেব্রাল কর্টেক্সের ভেতরের দিকে কতগুলো নিউক্লিয়াসের সমষ্টি; থ্যালামাস ও হাইপো থ্যালামাস। থ্যালামাস হলো রিলে স্টেশনের মতো, যা অনুভূতিগুলোকে এক সাথে জড়ো করে গুরুত্ব অনুসারে পরবর্তী প্রসেসিং এর জন্য কর্টেক্সের দিকে পাঠিয়ে দেয়। হাইপোথ্যালামাস হলো ক্ষুধা, আত্নরক্ষা, প্রজনন আচরণ এবং ঘুম ও জেগে ওঠার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র।
পনজ এবং মেডুলা অবলংগাটা হলো হিন্ডব্রেইন বা পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ; যার কাজ হলো আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস, হার্টের ছন্দ এবং রক্তের গ্লুকোজমাত্রা নির্ধারণ করা।
সেরেবেলাম:
হিন্ড ব্রেইনের আরেকটি অংশ হলো সেরেবেলাম; যারও ঠিক সেরেব্রামের মতো ডান ও বাম অংশ আছে। চলাফেরা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়া এবং শিক্ষণ ও অনুধাবনে সেরেবেলামের ভূমিকা আছে।
মেরুরজ্জু বা স্পাইন
ব্রেইনের নলাকার বর্ধিতাংশই হলো মেরুদন্ডের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়া মেরু রজ্জু বা স্পাইনাল কর্ড। এটি মাথার নীচের সমস্ত অংশ থেকে সেনসোরি তথ্য নিয়ে আসে। এটা ব্যথার অনুভূতির জবাবে রিফলেক্স প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সেনসোরি তথ্যকে ব্রেইনের ও সেরেব্রাল কর্টেক্সের দিকে পাঠিয়ে দেয়। এ ছাড়া, স্পাইনাল কর্ড থেকে উৎপন্ন নার্ভ তাড়নার সাহায্যে পেশী ও পরিপাকনালীর নাড়াচাড়া নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়ন্ত্রনের কিছু অংশ হয় রিফ্লেক্স প্রতিক্রিয়ার মতো করে, আবার কিছু হয় সেরেব্রাম এর ইচ্ছাধীন হুকুম অনুসারে।
নার্ভাস সিস্টেমের প্রধান শ্রেণিবিভাগ:
দুটি অংশ: সেন্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় (সিএনএস) এবং পেরিফেরাল বা প্রান্তীয় (পিএনএস)।
সিএনএস এর মধ্যে এই চারটি অংশ: ফোরব্রেইন, মিডব্রেইন, হিন্ডব্রেইন ও স্পাইনাল কর্ড। এর মধ্যে প্রথম তিনটি হলো ব্রেইনের অংশ যা মাথার খুলির মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, আর মেরু দন্ডের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় স্পাইনাল কর্ড।
পিএনএস গঠিত হয় নার্ভ ও নার্ভগুচ্ছ দিয়ে (যাকে গ্যাংগ্লিয়া বলে)।
ব্রেইন তার আদেশবাহী তথ্যকে স্পাইনাল কর্ডের মধ্য দিয়ে প্রান্তীয় নার্ভের দিকে পাঠিয়ে দেয়, যার সাহায্যে পেশী ও শরীরের ভেতরকার বিভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রিত হয়।
সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম সিএনএস এর সাথে আমাদের দেহের ওই অংশগুলোর সংযোগ স্থাপন করে যেগুলো বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করে। মেরুরুজ্জুকে উপর থেকে নীচে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। উপরের সারভাইকাল অংশের নার্ভ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় ঘাড় ও দুই হাত। এর পরে থোরাসিক অঞ্চলীয় নার্ভ নিয়ন্ত্রন করে বুকের অংশ। আরো নীচে লাম্বার ও স্যাকরাল অংশ সংযোগ স্থাপন করে পায়ের সাথে।
সোমাটিকের পাশাপাশি “অটোনমিক” বা স্বায়ত্বশাসিত নার্ভাস সিস্টেম সম্পর্কেও কিছু জানতে হবে। অটোনমিক এনএস এর মাধ্যমে দেহের ভেতরের অংগ বিশেষত কিছু গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থির কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হয়। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের আবার দুটি অংশ আছে: সিমপ্যাথেটিক এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক।
সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম যখন সক্রিয় থাকে তখন দেহ তার সঞ্চিত শক্তিকে খরচ করে বিপদ, চাপ বা যে কোন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য। আর প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম সক্রিয় হলে দেহ বিশ্রাম নেয়, ঘুমায় এবং শক্তি সঞ্চয় করে।